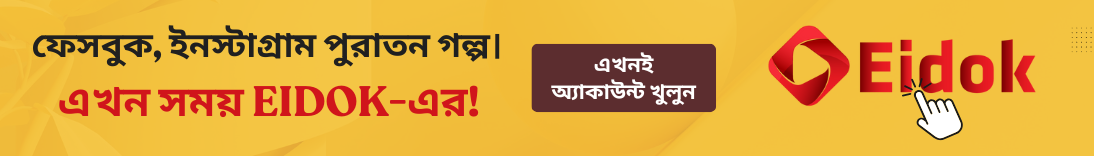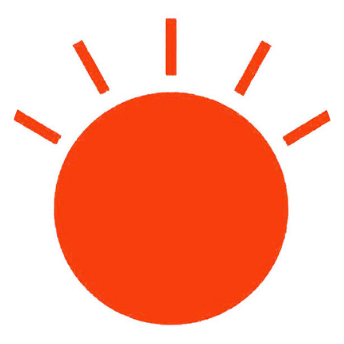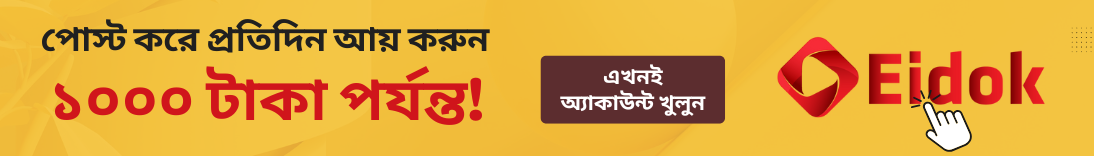বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২৪ সালের “৩৬ জুলাই” হয়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত মেরুকরণের মুহূর্ত। অনেকের চোখে তা ছিল এক অভ্যুত্থান, অনেকের কাছে পরিবর্তনের সূচনা। সেই সময় যে উদ্দীপনা, যে আবেগ, যে স্বপ্ন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এক বছর পেরিয়ে এসে সেটিই আজ যেন হয়ে উঠেছে এক ভারী নীরবতা, বঞ্চনা আর হতাশার প্রতিচ্ছবি।
এই পুরো সময়টাকে কেউ কেউ তুলনা করছেন ১৯৭২ সালের সঙ্গে—স্বপ্ন আর স্বজন হারানোর ভেতর দিয়ে রচনা হয়েছিল সে বছর। অথচ এবারকার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আর সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা যতটা ছিল, বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে ততটাই বেদনাদায়ক।
বিপ্লবের প্রতিটি দিন কেটেছিল নতুন দিনের স্বপ্নে। প্রশাসনের পরিবর্তন, দমন-পীড়নের অবসান, বৈষম্যের নিরসন—এই ছিল শ্লোগান। কিন্তু বাস্তবে প্রশাসন, আমলাতন্ত্র এবং পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষের ছবি মিলেছে বারবার। সরকার বদলেছে, নেতৃত্বের মুখ বদলেছে, কিন্তু ব্যবস্থার ভেতরকার যন্ত্রণা থেকে জনগণ মুক্তি পায়নি।
মাঠে যে কৃষকেরা রক্ত ঢেলেছেন, শহরে যে শ্রমিকেরা মিছিল করেছেন, পাহাড়ে যে সংখ্যালঘুরা জীবন দিয়েছে—তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ছিল নিস্পৃহ।
‘লাল জুলাই’–এর কথা বলা হয়েছিল—বৈষম্য কমিয়ে দেওয়ার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সংবিধান থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মৌলিক নীতিও হারিয়ে গেল। একবছরে গঠিত অসংখ্য কমিশনের বেশিরভাগই এড়িয়ে গেছে কৃষক, শ্রমিক, দলিত ও নারী ইস্যু। এমনকি ৪৪৫ পৃষ্ঠার শ্রম খাতের কমিশন রিপোর্ট জমা পড়লেও, তা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক আলাপই হয়নি।
অভ্যুত্থান-পরবর্তী নেতৃত্বের অনেকেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও কিছু করতে পারেননি। বরং নারীদের মৈত্রী সমাবেশে গালাগাল, স্বৈরাচারবিরোধী সংগঠকদের অনলাইনে লাঞ্ছনা, মামলার হুমকি ও মব-সহিংসতার বাস্তবতা দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
যাঁরা এক বছর আগে মাঠে ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিপ্লবের নেতৃত্বে—তাঁদের অনেকেই আজ দপ্তর প্রধান, মহাপরিচালক কিংবা উপদেষ্টা। কেউ কেউ আবার নতুন দল গঠন করেছেন—‘এনসিপি’। কিন্তু এই দলের আদর্শ, রাজনৈতিক অবস্থান ও সংগঠনিক কাঠামো আজও অস্পষ্ট। বরং এনসিপিকে ঘিরে বিতর্ক বেড়েছে—এটা কি জনগণের দল, নাকি আরেকটি নিয়ন্ত্রিত ‘কিংস পার্টি’?
নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টা পদ ছাড়ার মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা অনেকের জন্য প্রশংসনীয় হলেও, বাকিরা কেন এখনো নীরব—সেই প্রশ্ন আজও অনুত্তরিত।
নতুন নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। কিছু সমাবেশে এমনকি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হয়েছে, যা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে। এসব ঘটনাই এনসিপিকে ঘিরে নানা সংশয়ের জন্ম দিয়েছে।
এভাবে একদিকে গণ–অভ্যুত্থান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে নতুন নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোও সুযোগ নিয়ে ছাত্রনেতাদের ব্যর্থতাকে ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে ফেলছে।
শ্রমজীবীদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, ফ্রি বাস সার্ভিস, কম দামে ফ্ল্যাটের প্রতিশ্রুতি কেবল বাজেট বক্তৃতাতেই থেকে গেছে। বাস্তবে কোনো পরিকল্পনার রূপায়ণ হয়নি। ফেসবুক লাইভ বা টকশোতে বিপ্লবের গল্প যতবার বলা হয়েছে, ততবার মাঠে কিছু করা হয়নি।
ফলে যে বিপ্লব শুরুর কথা ছিল নতুন এক রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে, তা থেমে গেছে পুরোনো আমলাতন্ত্রের বাঁধনে।
আজকের বাংলাদেশ খুঁজছে তার নূরলদীনকে। সেই নেতৃত্ব, যে বাস্তবের বুকে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখাতে পারে, এবং তা বাস্তবায়নেও সক্ষম। হয়তো কোনো কালো পূর্ণিমায়, কোনো নিঃশব্দ ভোরে সেই ডাক আসবে। আবার দুঃখিনী মায়েরা তাঁদের সন্তান উৎসর্গ করবেন দেশের তরে। কারণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কখনো মরে না।
তবে সেই নতুন দিনের জন্য, নেতৃত্বকে হতে হবে পরিস্কার, দায়বদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অটল। বিপ্লবের স্মৃতি যদি এক বছরেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কীভাবে ফিরবে?
“৩৬ জুলাই” আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কেবল স্বপ্ন দেখানো যথেষ্ট নয়—স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস, দৃঢ়তা আর জবাবদিহিতা চাই। অন্যথায়, মানুষ তার স্বপ্নকে বুকপকেটে গুঁজে রেখে চুপ করে যায়। আর তা রাষ্ট্রের জন্যই হয় সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।