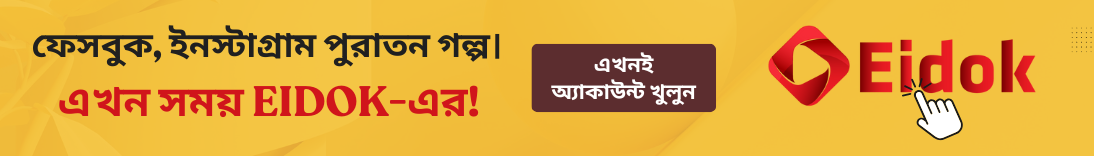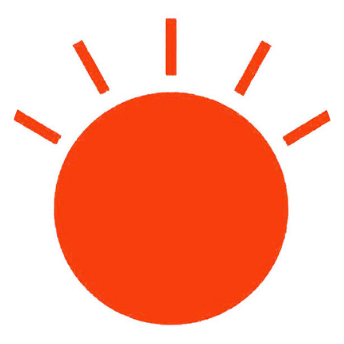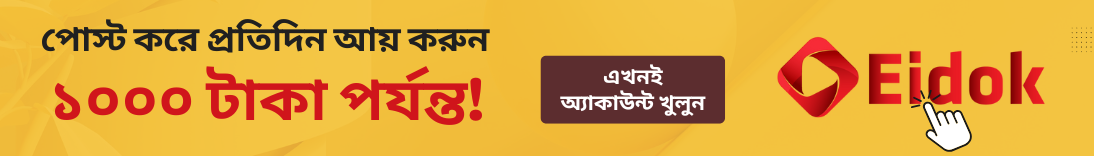ডেসক্রিপশন: এই বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে কেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হওয়া অর্থ যুক্তরাজ্য থেকে ফেরত আনার ব্যাপারে আলোচনার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সাক্ষাৎ হয়নি, যা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক প্রশ্ন তৈরি করে। স্টারমারের লেবার পার্টির প্রভাবশালী সদস্য টিউলিপ সিদ্দিকীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক এবং এই অর্থ পাচার তদন্তে তার নাম ঘিরে বিতর্ক—এই দুটি কারণ ছিল বৈঠকটি বাতিলের পেছনে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সাক্ষাৎ হলে লেবার পার্টির অভ্যন্তরে বিভাজন ও বিতর্কের ঝুঁকি ছিল, যা প্রধানমন্ত্রী স্টারমার রাজনৈতিকভাবে এড়িয়ে গেছেন।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের একজন বিশ্ববরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত, ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্বের জনক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। ২০২৪ সালের আগস্টে দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সরকার গঠিত হয় একটি অসাংবিধানিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, যেখানে পূর্ববর্তী সরকার বিরোধী দলের ওপর নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি এবং ভোটাধিকার হরণে অভিযুক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে, আপাতত একটি তদারকি সরকার পরিচালিত হচ্ছে যার নেতৃত্বে আছেন ড. ইউনূস।
২০২৫ সালের জুন মাসে ড. ইউনূস লন্ডন সফর করেন। তার সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাজ্যের সরকারের সহায়তা চাওয়া—বিশেষ করে সেখানে পাচার হওয়া বাংলাদেশি সম্পদ (যার পরিমাণ আনুমানিক \$২৩৪ বিলিয়ন) ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে। তিনি চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি নীতিগত ও কূটনৈতিক বৈঠক হোক, যাতে এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি একটি আন্তর্জাতিক নৈতিক চুক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্যার কিয়ার স্টারমার এই সাক্ষাতের অনুরোধ গ্রহণ করেননি। এই একটাই ঘটনা একাধিক জটিল প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।
প্রথমত, কেন একজন আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যিনি এখন একটি তদারকি সরকারের নেতা, তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন না? এ কি নিছক কর্মসূচির সঙ্ঘাত, নাকি এর পেছনে আছে গভীরতর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ?
এর জবাব খুঁজতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার- যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র। স্যার কিয়ার স্টারমার নেতৃত্ব দিচ্ছেন লেবার পার্টিকে, যারা সর্বদা মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান দেখানোয় বিশ্বাস করে। কিন্তু ড. ইউনূস যেহেতু একটি সরাসরি নির্বাচিত সরকারের নয়, বরং একটি জরুরি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় গঠিত সরকারের প্রধান, তাই তাঁর সঙ্গে উঁচুপর্যায়ের বৈঠক একটি সমস্যাজনক ‘নৈতিক সংকেত’ দিতে পারত। এটি ধরে নেওয়া হতো যে যুক্তরাজ্য একটি অনির্বাচিত সরকারের প্রতি তার রাজনৈতিক বৈধতা স্বীকার করছে- যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনভিপ্রেত ফল ডেকে আনতে পারত।
এখানে আরেকটি বিষয় জড়িত- টুলিপ সিদ্দিক। তিনি একজন প্রভাবশালী ব্রিটিশ এমপি, স্টারমারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনি। ২০২৪-২৫ সালে তার বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়, যার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের উৎস ও মালিকানা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে স্টারমার যদি ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতেন, তবে সেটি হতে পারত টুলিপকে ‘বলি’ হিসেবে চিহ্নিত করার একটা কৌশল, কিংবা এটিকে দেখা যেত ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের এক প্রকাশ হিসেবে। ফলে এই সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাওয়াই ছিল কূটনৈতিকভাবে নিরাপদ।
তৃতীয় দিকটি আরও জটিল। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কিছু বিরূপ প্রতিবেদন পেয়েছে। জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে- সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন, মিডিয়ার স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়া, এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যদিও এসব অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন, তবু যুক্তরাজ্য সরকার, বিশেষ করে একটি নতুন লেবার প্রশাসন, এরকম বিতর্কিত প্রেক্ষাপটে সরাসরি কোনও বৈঠকে অংশ নেওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না।
চতুর্থত, লন্ডনের NCA (National Crime Agency) ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি কিছু বিতর্কিত সম্পত্তি ফ্রিজ করেছে। এই অর্থের উৎস যাচাই না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের কোনো উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ড. ইউনূসের সঙ্গে আলোচনায় গেলে সেটি আইনি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ব্রিটিশ সরকার আইনি স্বাধীনতাকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়, আর তাই স্টারমার কোনওরকম ‘পলিটিক্যাল ফেভার’ দেখাতে চায়নি।
এখানে জনমত এবং ব্রিটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশি প্রবাসীদেরও একটি ভূমিকা আছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে একটি বড় অংশ এখনও আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল। অন্যদিকে, কিছু সংখ্যক তরুণ প্রজন্ম গণতন্ত্র ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ মতভেদ স্টারমারের জন্য স্পর্শকাতর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যেই পক্ষকে খুশি করতে যাবেন, অন্য পক্ষের বিরাগভাজন হবেন- এটি নিশ্চিত। তাই দেখা না করার সিদ্ধান্ত সেই দ্বান্দ্বিক চাপ থেকেও এসেছে।
এছাড়া টেকনিক্যাল বা সময়সূচির ব্যস্ততাও একটি প্রাসঙ্গিক কারণ হতে পারে, যদিও তা আপাত যুক্তির মতো মনে হয়, বাস্তবতাকে পুরোপুরি ধারণ করে না। ড. ইউনূস নিজে স্বীকার করেছেন যে স্টারমার তখন কানাডায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। তবে এমন বৈঠকের জন্য সময় বের করা প্রায় সব সময়ই সম্ভব, যদি কূটনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। ফলে এটি রাজনৈতিকভাবে ‘ডিপ্লোমেটিক নন-এংগেজমেন্ট’ হিসেবে ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত।
এখন প্রশ্ন হলো, এই সাক্ষাৎ যদি হতো- তবে কী ক্ষতি হতে পারত? বাস্তবতা হলো, ক্ষতির ঝুঁকি শুধু একক একটি সাক্ষাৎ থেকে নয়, বরং সেটির আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া থেকে আসে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলাদেশ সরকারের অনুগত প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তানের নজর, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভিন্নমত- এই সবগুলো বিষয় একযোগে আলোচনায় আসে।
তবে সমাধানের পথ একেবারে বন্ধ নয়। ব্রিটেন চাইলে ভবিষ্যতে একটি মধ্যপন্থা নিতে পারে। তারা চাইলে ড. ইউনূসের সরকারের সঙ্গে নিচু পর্যায়ের (mid-level) কূটনীতিকদের মাধ্যমে আলোচনা করতে পারে। তারা চাইলে একটি যৌথ মানবাধিকার তদন্ত কমিটি পাঠাতে পারে বাংলাদেশে, যেটি আন্তর্জাতিকভাবে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করবে। এছাড়া নির্বাচনকালীন পরিকল্পনার একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করাও যুক্তরাজ্যের ভূমিকা হতে পারে- যেটি রাজনৈতিক বৈধতার প্রেক্ষাপট তৈরি করবে।
এই সমগ্র পরিস্থিতি মানবিক ও রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী স্টারমার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক ও কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি তার সরকারের নীতিনিষ্ঠ অবস্থানের ফল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সিদ্ধান্তের চেয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়াও অনেক সময় একটি শক্ত বার্তা দেয়। এই ক্ষেত্রে তিনি 'নৈতিক নীরবতা'র মধ্য দিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন- গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে না।
অবশেষে, বলা যেতে পারে, ড. ইউনূসের সঙ্গে স্টারমারের দেখা না হওয়ার ঘটনায় কোনো পক্ষই পরিপূর্ণ জয় বা পরাজয় দেখেনি। এটি ছিল বাস্তবতার প্রতি এক নীরব স্বীকৃতি- যেখানে কূটনৈতিক পরিমিতিবোধ, নৈতিক সমঝোতা এবং রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ সবকিছুই মিলে গেছে একটি নিরপেক্ষ, কিন্তু গভীর সিদ্ধান্তে। এটা ছিল সঠিক মুহূর্তে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে না জানিয়ে বরং বাস্তবতা ও নীতির ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল।